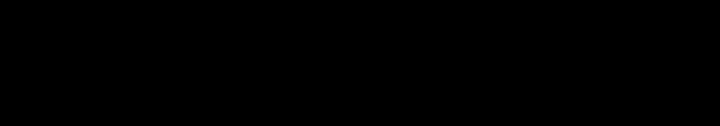আনন্দধামের পথে
কাজী সোহেল
সেই সকালগুলোর কথা ভাবলে আজও কেমন রোমাঞ্চ লাগে গায়। ডিসেম্বরের স্কুল ফাইনাল শেষে কোন এক আদুরে ভোরে মা ঘুম থেকে ডেকে বলতেন, ‘ওঠ, ওঠ নানুবাড়ি যাবি না!’ এতো স্কুলে যাবার জন্য ডাক নয়। এতো ভালোবাসাভূমির ডাক। তড়াক করে লাফিয়ে উঠতাম ঘুম থেকে। আমার ছোট ভাইটা রাসেল। ওকে একটু কসরত করতে হতো জাগাতে। মা আমাকে জাগিয়েই চলে যেতেন অন্যকাজে। আমি রাসেলকে নিষ্ঠার সাথে ঝাঁকিয়ে, পানি ছিটিয়ে তুলতাম ঘুম থেকে পাছে না আবার নানুবাড়ির যাত্রাশুরুতে দেরি হয়ে যায়। মায়ের হাতব্যাগ, আমাদের ছোট ছোট স্যুটকেস আর মায়ের প্লস্টিকের ঢাকনা ও ওপরে চিকন স্টিলের জোড়া হাতলের বাক্সোমতো নীল ঝুড়িটা গোছানো হলে আমরা যাত্রাশুরু করতাম। কী আনন্দ! কী আনন্দ!! শুধু ক্ষীণ একটা বেদনাবোধও থাকতো মহল্লার বন্ধুদের জন্য। ওরা এই ছুটিতে কতো জানি মজা করবে। যদিও নিশ্চিত জানতাম যে, নানুবাড়ির মজার তুলনায় সেগুলো কিছুই নয়। আসলে মানুষ বড্ড লোভী, সবই চাই তার। সেদিন রোজকার দেখা যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তটাাও বদলে যেতো। ভালো লাগতো বাস, ঠেলাগাড়ি, রিকশা, ভ্যান, বেবি ট্যাক্সি, ভিড় এগুলো দেখতেও। কখন আসবে আরাধ্য সেই ঢাকা-ঘোড়াশাল লেখা বাস। কখনো সিট পাবার জন্য আমরা গুলিস্থান চলে যেতাম। বেশির ভাগ সময়ই যেতাম আমি, রাসেল, আম্মা আর কোন একজন মামা সাথে থাকতেন পৌঁছে দেবার জন্য। তখন আমি, রাসেল খুব ছোট, কিন্ডারগার্টেনে পড়ি। নানু বাড়ি যাবো, শুনতেই আনন্দে ঝলমল করতাম তার কারন ছিলো সেই বাড়ি, সেই গ্রাম নানু, বুড়ুমাসহ অসংখ্য মামা, খালা, ভাই বন্ধু নানা নানুর আদরে পূর্ণ ছিল। সেখানকার প্রকৃতিও দারুণ, মনভোলানো।
বাসে আমাদের দুই ভাইয়ের জন্য কোন সিট নেয়া হতো না। কোলে করেই যেতাম। যেবার প্রথম আমার জন্য বাসে একটা সিট বরাদ্ধ করা হলো সেই মুহূর্তের ম্যাজিকে ‘বড় হয়ে যাওয়া’র আনন্দও ছিলো মনে রাখার মতো। বাস ডেমরা রোড দিয়ে কাঁচপুর পৌঁছুলে বিস্ময় নিয়ে দেখতাম, কাঁচপুর ব্রিজ কী রকম খাড়া প্রায় আকাশের মতো উচু হয়ে পেরিয়ে গেলো নদী। কী বিস্ময়! নদীতে লঞ্চ দেখলেই খুব সারেঙ হতে ইচ্ছে হতো আমার। এখনো হয়। নদীতে লঞ্চ চালাবার চেয়ে আনন্দময় কোন কিছুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে বলে তখন জানতাম না। বাস কাচপুর ব্রিজের ওপাড়ে গিয়ে থামলে কিছু লোক ওঠানামা করে। বাস কন্ডাক্টর ভাড়া চাইতে এলে মামা ইশারায় জানিয়ে দেয়, ‘আমরা ঘোড়াশাল যাবো।’ সরে যেতো কন্ডাক্টর। যেন আমরা বিশেষ কেউ। আমাদের কাছে তখন আর ভাড়া চায় না সে। শিশুদিনের সব কিছুতেই ভালো লাগা খুঁজে পেতো মন। একটু বড় হতে শুরু করলে করলে লোকের সে ভালো লাগা খোঁজার অভ্যাস চলে যেতে শুরু করে। কারো কারো সে স্বভাব বড়কালেও যায় না। যায়নি আমার।
বাস আবার চলতে শুরু করেছে। সেসময় অনেক বাসের মেঝেটা হতো কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি তাতে কিছু ফাঁকও থাকতো বা ভাঙ্গা। সেই ফোঁকর দিয়ে দেখতাম কী জোরে দৌড়ুচ্ছে আমাদের বাস তখন সাথে সাথে উলটো দিকে দৌড়ুচ্ছে রাস্তার দু’পাশের গাছগুলোও। দু’পাশেই আদিগন্ত ফসলের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ইট ভাটার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কোথাও কোথাও কোন মিলের বেয়াড়া বড় বিল্ডিং অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেসবে আমার নজর থাকতো না তেমন, আমার দৃষ্টি বেশি সময়ই আটকে থাকতো রাস্তার পাশে সমান্তরাল খালে। তাতে ভাসতে থাকা কচুরিপানা, সাঁতারকাটা হাঁস বা কালে ভদ্রে লাফিয়ে ওঠা মাছ বিচরণ করতো আমার নয়ন জোড়ায়। সাধারনত যেতাম কুরবানির ঈদে বা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষার শেষ হবার পরে। কী দারুণ নীল তখন আকাশ, ছোট শিশুর দলের মতো শুভ্র মেঘরা ভেসে বেড়াতো আকাশের এদিক-সেদিক। ভুলতা/গাউসিয়া এলে বাস থামতো বেশ কিছুক্ষণ। নানারকম ফেরিওয়ালা, হকার উঠতো বাসে। বারো মশল্লা চানাচুর, বাদাম ভাজা, দাঁতের মাজন, লজেন্স, আমড়া, চিরুনি, শ্রীপুরের বড়ি যেনো চলমান বায়স্কোপ। কতো রকম কথা, কতো রকম ভঙ্গিমায় তারা পণ্যের গুণগান গাইতো। আমি খুব অবাক হতাম, এতো ভালো ভালো জিনিষ তবু লোকে প্রায় কিনছেই না, বাসের লোকগুলো এমন কেন!! মায়া হতো আমার। বেশ সমন্বয় থাকতো হকারদের মাঝে। বেচা বিক্রি নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে এমন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি কিনতাম বারো মশলা ঝাল চানাচুর বা ঝালটেস চানাচুর, কী যে ভালো লাগতো!! মা দু’ভাইকে চারটাই কিনে দিতো। রাসেল খেতে পারতো না পুরো। ওটাই যা লাভ ছিলো আমার। ঝালটেস চানাচুরওয়ালার কাছে অতোগুলো চানাচুর প্যাকেট দেখে খানিক হিংসাও হতো। আম্মা নিতো খোসা ছাড়ানো তেলে ভাজা বাদাম। তিনিও খেতেন বেশ মজা করেই আমাদের সঙ্গে। আমি সেদিকেও মাঝে মাঝে হাত বাড়াতাম। দু চারটি দানা যা পড়ে হাতে তাই লাভ। হা হা হা।
ভুলতা/গাউছিয়ার আশেপাশে একটা সাধারণ দৃশ্য ছিলো কাপড় রঙ করে রোদে দেবার দৃশ্য। মন দিয়ে দেখতাম বড় মাটির গামলায় থাকতো রঙ। তাতে চোবানো হতো কাপড়। বিশেষ কায়দায় বাঁশে ঝোলানো দড়িতে মেলে দেয়া হতো কাপড় শুকাবার জন্য। পরের স্টপেজ পাঁচরুখি এলে দুইভাই খানিকটা উত্তেজিত হয়ে তাকাতাম বাইরে। রাসেলকে বলতাম একটু ভাব নিয়ে,
‘দ্যাখ দ্যাখ, বর্ষাকালে এহান দিয়াই কিন্তু আমরা পাঁচগাঁও যাই।’
‘এহ আমিও চিনি’ বলতো রাসেল।
ও আমার চেয়ে পাক্কা দুই বছরের ছোট তবু ওর সবকিছু মনে থাকে কেন? সেজন্য খানিক হতাশ হতাম। পাঁচগাঁও যাবার পথ- সেও ছিলো দারুন। নৌকা দিয়ে বিলের মধ্যে শাপলা তুলতে তুলতে যাওয়া। সাথে থাকতো সাধারনত মিষ্টি রসে ভরা সে এলাকার বিখ্যাত তালের বড়া আর পাউরুটি। যাক বাস আবার চলতে শুরু করতো যাত্রি ওঠানামার পর। এবারের স্টপেজ পুরিন্দা। শুকনার দিনে পাঁচগাঁও যাবার রাস্তা। পাঁচগাঁও আমাদের নানাবাড়ি। আর যেখানে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের, সেটা আমার নানুর বাবার বাড়ি। ছেলেবেলা অনেক ছুটি আমরা সেখানে কাটিয়েছি। আমাদের প্রিয় শৈশব ছড়িয়ে আছে সেখানে। পুরিন্দার পরের স্টপেজ মাধবদী মানে আমাদের আসল স্টেশন। পূর্বপুরুষের বাড়ি, বাবার বাড়ি, আমাদের বাড়ি যেতে নামতে হয় এখানেই। গ্রামের নাম বালুসাইর। কী মিষ্টি না নামটা? বাড়ি যাবার রাস্তাটা ভালো করে দেখেই চোখ আর মন চলে যেতো ডানে। সেখানে একটা দারুণ মিষ্টির দোকান আছে জানি। বড়কাকু, মেঝকাকুর সাথে গিয়েছি সেখানে। বালুসাইর যাবার রাস্তাটা একদম অন্যরকম সুন্দর। দুইপাশেই আদিগন্ত ফসলের মাঠ। মাঝ দিয়ে একে বেঁকে চলে গেছে আমার বাড়ি যাবার রাস্তা।বড় মায়া! বড় মায়া!! চলুন নানুবাড়ির দিকেই মন দেই আজ। বাস এগিয়ে যাচ্ছে। মাধবদী পেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে রাস্তা। মন দিয়ে দেখতাম তাদের জীবনযাপন, শহরের চেয়ে এই সবুজ অনেক বেশি টানতো আমাকে। কী আপন লাগতো সেই সব!
বাসের সিটে বসে মজার একটা খেলা খেলতাম। সামনের সিটের লোহার পাইপ ধরে। মনে মনে ভাবতাম, বাস চালাচ্ছি আমিই। পথের আঁকাবাঁকা দেখে আমিও ডানে-বায়ে ঘোরাতাম শরীর, হেলে পড়তাম নিজেও। কী যে মজা লাগতো শুধু ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক করলে রসভঙ্গ হতো। পরের স্টপেজ পাঁচদোনা এলে রাস্তা দুভাগ হয়ে যেতো। একটা ঘোড়াশালের দিকে আর একটা নরসিংদীর দিকে।
আমাদের বাস বাদিকের রাস্তা ধরে এগোয় চলে, হ্যাঁ ছোটবেলায় সব নিজেদের হয়ে যায় তার জন্য কোন টাকাপয়সা লাগে না। বাস আরও বেশ কিছুক্ষন চলার পর ডান পাশে যখন রেললাইন চলে আসতো। মনে হতো এই তো কাছে চলে এসেছি। মন দিয়ে দেখতাম উচু রেললাইন। আর যদি রেলগাড়ি পেয়ে যেতাম তাহলে তো সোনায় সোহাগা। রেলের জানালায় উঁকি দেয়া মুখগুলোকে অনেক ভাগ্যবান মনে হতো রোল চড়তে পারছে বলে। রেলের শব্দের তালে তালে শব্দ করা শুরু করে দিতাম … কুউ উ … ঝিক ঝিক… কুউ উ … ঝিক ঝিক……
যাদের গল্প করার মতো শৈশব নেই তাদের জন্য মায়া হয়। তা সে ধনী হোক বা গরীব সে আসলে দরিদ্র। একসময় বাস এসে পৌছোয় গন্তব্য ঘোড়াশাল বাসস্ট্যান্ডে। সবাই নেমে গেলেও মা আমাদের নামতে দিতেন না। দু’হাতে দুই ছেলেকে ধরে রাখতেন তিনি। যদিও আমরা মোটেও অমন দুষ্ট বাচ্চা ছিলাম না। বাস ঘুরিয়ে আবার ঢাকামুখি হয়ে একেবারে থেমে যেতো। তখন ভাড়া মিটিয়ে মা নামতেন আমাদের নিয়ে। শুরু হতো রিকশাওয়ালাদের হাকডাক, এই ফুলেশ্বরী, বিরিন্দা, পলাশ, গাঙপার… রিকশাওয়ালারা অনেকে চিনতো। তাই ওরা ওঠানোর জন্য বিরক্ত করতো। আম্মা চাইতেন রিকশায় যেতে, আমরা দুই ভাই চিৎকার করতাম নৌকা, নৌকা। রাজনৈতিক স্লোগান নয় সেটা, হা হা হা, নৌকা চড়ে নানুবাড়ি যাবার সমন্বিত নিবেদন মায়ের কাছে। বেশিরভাগ যাওয়া হতো রিকশায়। মাঝে মাঝে আম্মা রাজি হতেন নদী পথে যেতে। আহা কী আনন্দ হতো তখন! রিকশায় করে পাঁচ মিনিটে নদীর পাড় চলে যেতাম। মাথার উপরে প্রায় আকাশছোঁয়া বিস্ময় হয়ে দেখা দিত নদীর বুকে ‘ঘোড়াশাল রেল সেতু’ তাকিয়ে থাকতাম দুই ভাই বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে। তারপর দেখে বেছে একটা সুন্দর, বড়, ছইওয়ালা নৌকাতে উঠতেন মা। আমাদের সাথে থাকতো একটা দুই স্পিকারের ক্যাসেট প্লেয়ার আর ১৭” ফিলিপ্স সাদাকালো টিভি। নৌকাতে বসেই মা বারবার মাঝিকে বলতেন নদীর কিনারা ধরে যেতে। সাঁতার না জানা মা পানিকে খুব ভয় পান। আর আমরা মায়ের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে বলতাম এক গভীর দিয়ে যান।
তখন নৌকায় বিরক্তিকর শব্দের ইঞ্জিন লাগেনি। মাঝি গান না শোনালেও বৈঠার ঝুপ ঝুপ বাড়ি পড়তো নদীর জলে, চমৎকার ছন্দে। হালকা ঘোলাটে শ্যাওলাগন্ধি নদীর জলে তখন ছোট ছোট ঢেউয়ের নাচন। নদীর জলেও রয়েছে নানা রকম রঙের খেলা। সব নদীর জলের একটা মূল রঙ থাকে, তাতে গভীরতা বাড়লে বা মাঝের দিকে গেলে রঙ বদলায়। নদীতে নীল আকাশের ছায়া, গোমড়া মুখি আকাশের ছায়া পড়লে রঙ বদলাতে থাকে। সাদা মেঘ, ছাই মেঘ, কালো মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড়ের আগে-পরে নদীর রঙের বিচিত্র খেলা চলে। শুধু নদীকে ভালোবাসলেই সে রঙ দেখা সম্ভব। শীতলক্ষ্যা আমার দেখা প্রথম নদী। আমার প্রথম প্রেম।
যাক এক মায়াময় ঢেউভাঙ্গা শব্দ করে হেলে দুলে নৌকা চলছে নানুবাড়ির ঘাটের দিকে। যেতে যেতে দেখতাম জেলেদের নদীতে জাল ফেলা, গুণ টেনে নিয়ে যেতে দেখতাম বড় মালবাহী নৌকা। নদী পারাপার হওয়ার গুদারা, কিম্বা ছোট্ট কোষা নৌকা নিয়ে নদী পাড় হওয়া কিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অপার বিস্ময়ে। ঝাঁকালো শ্যাওড়া গাছ ও হিন্দু পাড়ার ঘাট এলেই আমি নৌকার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তাম। বকুনি দিতেন আম্মা। তখন কে শোনে কার কথা! নামলেই নানু, বুড়ুমা আদরের ঝাঁপি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। মায়ের বকুনি তখন পাত্তাই পাবে না। উলটো তাঁর ধমক খাবার সমূহ সম্ভাবনা।
‘নৌকা ভালো কইরা ভিড়ান ঘাটে ‘ বলতেন মা। সবাই নেমে গেলে মাঝি বা তার সহকারি মাঝি নৌকা শক্ত করে ধরে রাখতেন মা ধীরে সুস্থে খানিকটা ভয়ে ভয়ে নামতেন পাড়ে। পাড়ে নেমেই দিতাম ছুট। তবু কি করে যেনো আমাদের পৌঁছার আগেই খবর পেয়ে যেতো নানু বুড়ুমাসহ অনেকে। আসতে শুরু করতেন বাংলাঘর ছাড়িয়ে, উঠান ছাড়িয়ে নদীর পাড়ের দিকে। কে আগে শুনেছে তাই নিয়ে শুরু হতো জড়ো হওয়া স্বজনদের উচ্ছসিত কথাবার্তা। সেখানকার সবাই আপন, সবাই ভালোবাসার মানুষ। মামা খালা নানা নানু সবাইকে নিয়ে যেনো আপন সমাবেশ। যেখানে নামতাম এই কয়েক কদম এগুলেই ছোট্ট ফুলেশ্বরী বাজার। শুরুতেই সেলুন দোকানের অধীর মামা থেকে শুরু করো শেষ প্রান্তে যে স্কুল তার শিক্ষিকা আরেফা খালাম্মা অবধি সকলেই আত্মীয়, আপনজন নয়তো প্রিয়জন। সান্তানপাড়া। নামটায়, গ্রামটায় ছড়িয়ে আছে আদর ও ভালবাসার ঘ্রাণ! রাতেই পিঠা করতেন নানু। আশেপাশের বাড়ি থেকে সবাই আসতো ঘরে, মাটির বারান্দায়। আমরা দুইভাই আধা শহুরে চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখতাম বালির উঠোনে চাঁদনী রাতে গাছের ছায়ার খেলা আর জোনাকির উল্লাস। শুরু হয়ে যেতো আনন্দ উৎসব।
লেখকের নোট:- লেখাটির পরিসর বৃদ্ধিতে Sangita দারুণ উৎসাহ দিয়েছে …