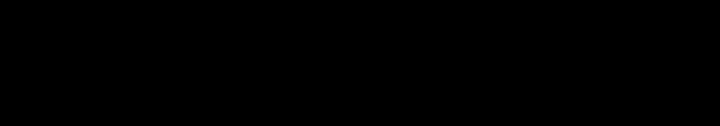নিউ অন্নপূর্ণা ভাতের হোটেল
(একটি বেলাগাম প্রতিবেদন)
মেনুবোর্ড–
শৈশবেই কেন জানি না হাটে-বাজারে, রেলস্টেশন কিংবা বাসস্ট্যান্ডের আশেপাশে থাকা হোটেলগুলো খুব ভালো লাগত আমার। শৈশব মানেই যেহেতু অপরের অঙ্গুলি হেলনে বন্দি এবং অজস্র বঞ্চনার সমাহার তাই কখনও ওসব জায়গায় পাত পেড়ে বসার সুযোগ পাইনি। এমন কী কৈশোরেও নয়। বাড়ির ভাত ছেড়ে দিয়ে কেউ হোটেলে ভাত খায় নাকি! লোকে দেখলে কী বলবে! এমন কী বেড়াতে গিয়েও সে সুযোগ মেলেনি। কারণ তখনকার দিনের মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল আক্ষরিক অর্থেই মধ্যবিত্ত। এখন সংজ্ঞাটা অনেক বদলে গিয়েছে। বৃত্তটা বড় হয়ে গিয়ে যে উপার্জন সীমার মানুষদের প্রবেশাধিকার দিয়েছে তাদের আমরা সে সময় বড়লোক হিসেবেই চিনতাম। সুতরাং আমাদের বেড়াতে যাওয়া মানে কোনো আত্মীয়বাড়ির উৎসবে যোগ দেওয়া। বাড়ি থেকে ভরপেট খেয়ে, সফরকালীন খাবার গুছিয়ে রওনা দেয়া এবং পৌঁছে যাওয়া মাত্র উৎসব বাড়ির টেবিল আলো করে বসে পড়া। এর মধ্যে হোটেল ঢোকে কিভাবে?
সুতরাং অধরা ওই হোটেলগুলোর সামনে দিয়ে যেতে যেতে সতৃষ্ণ নয়নে চাখতাম ওদের। দর্শনেন সিকি ভোজনং। আমার সেই দর্শনে ‘ফিলোস’ অর্থাৎ বন্ধু, ভালোবাসার পাত্র ছিল হোটেলের সামনে বসে কুটনো কোটা, মাছ-মাংস ধোয়া, জলের ড্রাম ভর্তির কাজে ব্যস্ত থাকা পাত্র-পাত্রীরা তো বটেই এমন কী সাইনবোর্ড, সামনে টাঙিয়ে রাখা মেনুবোর্ডকেও বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত করিনি। ভেতরে টেবিল পেতে বসে থেকে দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলা ম্যানেজারবাবুটিকে তো রীতিমত মহাপুরুষের প্রাপ্য সম্মান দিতাম।
বাকি রইল যে ‘সফিয়া’ অর্থাৎ প্রাজ্ঞতা, সেটাতে পৌঁছতে গেলে যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেটার অভাবে আমাকে অনুমানের আশ্রয় নিতে হোত। বলাবাহুল্য সেই অনুমান কখনোই আমাকে হতাশ করেনি।
প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধুই কি দেখেছি? কখনও সুখাদ্যের ঘ্রাণ পাইনি কি?
উত্তর–অবশ্যই পেয়েছি। তবে লালায়িত হইনি। কারণ কোনদিনই আমি ভোজনবিলাসী ছিলাম না। আমার ক্ষুৎ চেতনা বরাবর খিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
থাক সেই ব্যক্তিগত বিবৃতি। আপাতত বলার এটাই যে ওই দর্শন মারফত আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, ওরকম একটা ভাতের হোটেল খুলতেই হবে আমাকে। আমিই সাত সকালে বাজারে যাব ঢাউস ব্যাগ নিয়ে।রাঁধুনি আমার কাছেই জানতে চাইবে, সর্ষে ইলিশ নাকি বেগুন ইলিশ। এরপর জল, থালা, নুন, প্রথম হাতা ভাত সবকিছুই পরিবেশিত হবে আমার তত্বাবধানে। এমন কী ভাতের শেষ কণাটিও চেটেপুটে খেয়ে, হাত ধুয়ে তৃপ্ত খরিদ্দার আমার সামনে রাখা পাত্র থেকে মৌরি চিবুতে চিবুতে আমাকেই জিজ্ঞেস করবে , ক্হতো হ্হলোহ?
যদিও পরবর্তীতে ওরকম হোটেলে অজস্রবার খেয়েছি। চোখ মেলে তো দেখেইছি, কান পেতেও শুনেছি ওদের অন্দরমহল এবং বাহিরমহলের কথাবার্তা। তাতেও স্বপ্ন তো ভাঙেইনি বরং গাঢ় হয়েছে। পড়েছি–আদর্শ হিন্দু হোটেল। স্বপ্ন দৃঢ় হয়েছে। তবু পারলাম কই? জীবনভর অজস্র ব্যর্থতার মধ্যে ওটাও একটা, ওই হোটেল খুলতে না পারা। একটা অতৃপ্তি আজীবন কুরে খেয়েছে।
অবশেষে স্বপ্নপূরণ। আটান্নর গন্ডি পেরিয়ে ঊনষাটের খোপে লাফ দিতে দিতে খুলতে পারলাম নিজস্ব হোটেল।নিউ অন্নপূর্ণা ভাতের হোটেল। হোক না ভার্চুয়াল, তাতে কি যায় আসে? এই দুঃসময়ে জীবনটাই তো ভার্চুয়াল হয়ে গিয়েছে। ভার্চুয়ালি লিখছি, পড়ছি, আড্ডা দিচ্ছি, এমন কী নিন্দা, ঘৃণা, সম্মান, অসম্মান, প্রতিবাদ, সমর্থন, সামাজিক দায়, প্রেম, পরকিয়া, লাম্পট্য , সবকিছুই ভার্চুয়ালি করছি। তাহলে আমার এই ভার্চুয়াল হোটেলের মালিক হওয়াটা হাস্যকর হবে কেন?
হয়ত লকডাউন এবং সামাজিক সুরক্ষাবিধিকে মান্যতা দিতে নিয়মিত হোটেলের দোর খুলতে পারব না। তবে যেদিন খুলব, অনুগ্রহ করে হে মাদাম এবং মসিয়েঁবৃন্দ, আপনারা রসনা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে যাবেন। নুন, মিষ্টি, ঝাল সংক্রান্ত পরামর্শ দেবেন শুধু আমাকেই কেননা আমার এই হোটেল ওয়ান ম্যান শো।
২.
“পড়ুন হাসির রাজা সুকুমার রায়ের কবিতা–খাই খাই করো কেন? আহা মরি বোসো রে।”
সাতটা চল্লিশের কিংবা চারটা ত্রিশের আপ ট্রেন হলে হয়ত খেয়াল করতাম না। গিজগিজে ভিড় এবং তার ভেতর দিয়েই জায়গা বের করে অসংখ্যা হকারের বারবার যাতায়াতে যে বিরক্তি উছলে ওঠে তাতে অত খেয়াল করার মতো সময় কোথায়? কিন্তু এটা দশটা দশের ডাউন। সহযাত্রীর সংখ্যা মেরেকেটে জনা পাঁচেক অথবা সাতেক। তাদের প্রত্যেকের দশা হেঁটমুন্ড। এবং ঊর্দ্ধপদও বলা যেতে পারে কারণ প্রত্যেকরই পা দুটো সামনের বেঞ্চে তুলে রাখা।
ট্রেন ছুটবে অথচ হকার থাকবে না, ব্যাপারটা যেহেতু চলাচলকে অপমান করা তাই সম্মান রক্ষার্থে কয়েকজন দায়সারা উঠেছিল। কিন্তু ঝালমুড়ি, ছোলাবাদাম, কলা তো বটেই এমন কী গরম চা-ও পারেনি হেলে পড়া মাথাগুলো সোজা করতে। অগত্যা দায়িত্বটুকু পালন করেই দু-তিন স্টেশন পরে নেমে গিয়েছে তারা। পিঁপড়ের মুখে মুখে খবর পৌঁছে যাওয়ায় পরবর্তীতে আর কেউ ওঠেনি। সহযাত্রীরা ব্যস্ত থাকতে পেরেছে ঝিমুনি প্রকল্পে, আর আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজা-উজির মারা ভাবনায়।
এমন একটা সময় যখন হাওড়া মোটে পাঁচ স্টেশন দূরে তখন বই হাতে এই ভদ্রলোক এবং ওই ঘোষনা–“পড়ুন হাসির রাজা সুকুমার রায়ের কবিতা–খাই খাই করো কেন? আহা মরি বোসো রে।”
যথারীতি আমার ভ্রু কুঁচকে উঠেছিল। কড়া চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম বয়স্ক মানুষ। চেহারার ধরণটা আমরা যেটাকে চলতি কথায় প্যাঙা বলি, তেমনটা। মাথায় এলোমেলো চুল এবং হাতে একগোছা চটি বই।
ভদ্রলোক ফের হাঁকলেন, সাপুরাম বাপুরে/ কোথা যাস সাপুরে/ আয় বাবা বসে যা/ দুটো ভাত খেয়ে যা।
এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আমার, এই যে শুনুন।
ডেলি প্যাসেঞ্জারির সূত্রে যদিও জানা আছে হকারদের সঙ্গে লাগতে নেই তবু স্বরে কর্কশতার অনুপ্রবেশ রুখতে পারলাম না।
ভদ্রলোক হাসিমুখেই এগিয়ে এলেন। বইয়ের গোছা বাড়িয়ে জানতে চাইলেন, কোন বইটা লাগবে স্যার?
দেখলাম সবকটা বইই সুকুমার রায়ের। এবং বটতলা প্রকাশনী। ভাবলাম হয়তো বেচারির দোষ নেই। বইতে হয়ত উল্টোপাল্টা ছাপা হয়েছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, দুটো ছড়াই নির্ভুল ছাপা রয়েছে।
–বই বিক্রি করছেন, ভালো কথা কিন্তু ছড়া বলার প্রয়োজনটা কিসের?
–ছড়ার বই বিক্রি করছি ছড়া বলব না! তাছাড়া কজন জানে বলুন তো সুকুমার রায়ের নাম?
ভদ্রলোকের মিথ্যে দম্ভ ভেঙে দেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।
–ভুলভাল বলার চে নাম না জানাও ভালো।
–কিসের ভুলভাল?
–আপনি যেগুলো বলছেন সেগুলো তো ভুলভাল। বলতে হলে সঠিক লাইন বলুন।
ভদ্রলোক এতক্ষণে আমার দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, সুকুমার রায়ের আবার ভুলভাল কী স্যার? ভুল নিয়েই তো ওঁর জগত ছিল।
এরপর আমার পক্ষে চটে ওঠাটাই ছিল স্বাভাবিক। সুকুমার ননসেন্স রাইমের চর্চা করেছেন বলে এক ননসেন্স নিজের খেয়াল খুশী মতো আউড়ে যাবে?
কিন্তু পারলাম না চটে উঠতে। দুটো কারণে। কারণ নং ১- ভদ্রলোকের কন্ঠস্বরের দৃঢ়তা। কারণ নং ২–ওর ঠোঁটে লেগে থাকা চিলতে হাসিটুকু।
–কী রকম বিক্রি হয়?
–কাল পাঁচটা হয়েছিল। আজ ফক্কা।
–অন্য কিছু ফিরি করেন না কেন?
— কি?
–যেটা সবাই কিনবে।
–কি সেটা, পাউরুটি আর ঝোলাগুড়?
এরপর কথা চলে না। এই রসিককে সঙ্গ দেয়ার মতো রস আমার ভেতরে নেই বুঝতে পেরে চুপ করে যাই।
ভদ্রলোক বললেন, চলি। সামনে হালুয়া স্টেশন আসছে, নেমে পড়ব।
ফের অবাক হলাম, হালুয়া স্টেশন!
–আরে, কেমন ডেলি প্যাসেঞ্জার আপনি! লিলুয়া আর হাওড়ার মাঝখানের স্টেশনটার নাম জানেন না?
অনেকক্ষণ চিন্তা করার পরও অমন কিম্ভুত স্টেশনের নাম মনে পড়ে না। হাওড়া স্টেশনে ঢোকার সিগন্যাল না পাওয়া অবধি ট্রেন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু ওখানে স্টেশন কোথায়!
–স্টেশন মানে কি শুধুই প্ল্যাটফর্ম আর কালো কোট, দাদাভাই? যেখানে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রতিটা ট্রেন দাঁড়ায় সেটাই স্টেশান।
এরপর সত্যি সত্যিই ট্রেনটা দাঁড়িয়ে যায়। ভদ্রলোক সাবলীল ভাবেই নেমে পড়েন অনেকটা নিচের রেললাইনে।
জানলার শিকে কপাল ঠেকিয়ে অহেতুক জিজ্ঞেস করি, কে কে আছে বাড়িতে?
ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন।
–আমরা দুজন। আমি আর সুকুমার।
এরপর ছড়া পাঠ করতে করতে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকেন সুকুমারের সঙ্গী। একটার পর একটা লাইন টপকে চলে যান অনেকটা দূরে কিন্তু কী আশ্চর্য ছড়া অস্পষ্ট হয় না। বাতাসে ভর করে সেই ছড়া ভেসে আসতে থাকে, আসতেই থাকে। জানলায় মাথা রেখে আমি শুনি–
মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কন্ঠ পুরে ।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা ।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপ্ন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে
ছুটলে কথা থামায় কে
আজকে আমায় ঠেকায় কে….
৩.
আমাদের শৈশবে আলোর চে অন্ধকারের আধিপত্য ছিল অনেক বেশী। আলো বলতে যদিও বিজলি বাতির কথা বলতে চাইছি কিন্তু বহিরঙ্গের আলোক তরঙ্গ বোধহয় অন্তরঙ্গে নিভে থাকা বাতিটাকেও জ্বালিয়ে দিতে পারে।
তখন বেশীর ভাগ বাড়িতেই লন্ঠন ভরসা। এর একটা কারণ অবশ্যই আর্থিক সমস্যা। যুদ্ধ, উদ্বাস্তু, অপরিকল্পিত অর্থনীতি ইত্যাদি প্রভৃতি নানা কারণে সেসময় দারিদ্র ছিল ভয়াবহ। তাই বিদ্যুৎ ছিল বেশির ভাগের কাছেই বিলাসিতা।
এই বিলাসিতা বিষয়েও দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। হয়ত দারিদ্রের সঙ্গে পিঠোপিঠি বসবাসের কারণে মধ্যবিত্তরাও সেসময় বিলাসিতাকে বড্ড ভয় পেত! বাজার-হাটে তখন মুখে মুখে যে সংলাপগুলো খুব ঘুরত সেগুলো ছিল– দিনকাল খুব খারাপ। আরও খারাপ দিন আসছে। আর বাঁচা যাবে না।
বিলাসিতার ডাক নাম ছিল–বাবুগিরি। বেশি বাবুগিরির অর্থ লক্ষ্মীদেবীকে অসম্মান করা। আর দেবী কুপিতা হলে পরিণতি কী হয় সেটা তো পাঁচালিতেই স্পষ্ট লেখা ছিল। সুতরাং সাধু সাবধান।
মনে আছে, একটা কাচের গ্লাস কিংবা কাপ হাত ফস্কে ভেঙে গেলে সংসারে যে হায় হায় রব উঠত সেটা প্রায় মৃত্যু শোকের তুলনীয় ছিল।
আগেই বলেছি আজকের তুলনায় তখন সস্তাগন্ডার দিন থাকা সত্বেও ভয়াবহ দারিদ্র ছিল চারপাশে। কিন্তু ওই দারিদ্রভীতি! কেন জানি না আজ মনে হয়, হয়ত অন্ধকারের দাপট এই আতঙ্ককে ভাত-জল জোগাতো!
তাছাড়া শুধু তো ওই আতঙ্কটাই নয়, আরও কত আতঙ্কই না সেসময় আমাদের সঙ্গী ছিল। সন্ধে নামলেই চারপাশে গিজগিজ করত অপদেবতারা। যখন তখন যার তার ওপরে চেপে বসত। তাদের জব্দ করতে শরণাপন্ন হোতে হোত তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীদের। তাদের মধ্যে নারায়ণের ভোগভাগ্য ছিল রীতিমত ঈর্ষণীয়। পাড়ায় এমন উঠোন ছিলই না যেখানে হরির লুঠ হয়নি। নিমন্ত্রণের কোনো বালাই থাকত না। কারণ নারায়ণ পুজোর কথা শুনলেই যেতে হবে। নাহলেই অকল্যাণ। আমাদের কাজ ছিল হাততালি দিয়ে “ চিনি সন্দেশ ফুল বাতাসা/ মন্ডা জোড়া জোড়া” গাইতে গাইতে কড়া নজর রাখা কখন বাতাসা ছেটানো শুরু হয়। কেউ কেউ অল্প বয়সেই লোফালুফিতে উস্তাদ হয়ে উঠেছিল। আমার ভাগ্যে জুটত মাটি মেশানো বাতাসার গুঁড়ো আর হাতে-মুখে আঘাত।
নিমন্ত্রণের কথায় মনে পড়ে গেল আরেকটা ঘটনা। এক দুপুরে আমাদের বাড়িতে হাজির পাড়ার একজন মহিলা। ওঁর ছেলের নামও ছিল অলোক। উনি স্বপ্ন দেখেছেন, একই নামের কোনো ছেলের মায়ের হাতে ভাত না খেলে ওঁর ছেলের অকল্যাণ হবে।
না, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে দু মুঠো ভাতের লোভে উনি অমন একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। কারণ ওদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল। সে যা-ই হোক, যেহেতু বিনা নিমন্ত্রণে এসেছিলেন তাই বাড়তি বন্দোবস্ত কিছু করা যায়নি কিন্তু ঘটনাটা চাক্ষুষ করতে এত পড়শি হাজির হয়েছিল যে সামান্য ডালভাতই উৎসবের রূপ নিয়েছিল। না, তাদের কারুর ছেলের নাম ‘অলোক’ ছিল না। “লোক”ই নয়, এমন খারাপ নাম রাখার কথা কেউ ভাবতেই পারেনি। ভাগ্যিস ভাবেনি নাহলে বাবার ওপরে খুব চাপ পড়ে যেত।
গল্পটা বললাম এটা বোঝাতে যে সেসময় অলৌকিকতা ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমরা যেহেতু উৎস জানতে আগ্রহী ছিলাম না তাই যুক্তি তক্কের ধার ধারতাম না। আমাদের সম্পদ ছিল শুধুই গপ্পো। আর ছিল কথায় কথায় কপালে হাত ঠুকে প্রণাম করে সবাইকে তুষ্ট রাখা। গুরুজন এবং দেব-দেবীরা তো বটেই গাছ-ফুল-পাখি-পাথর-বই-খাতা-পেন্সিল আরও অনেক কিছুই ছিল আমাদের শ্রদ্ধা তালিকায়। শিক্ষা এবং সংস্কারের ভেতর কোনো বিরোধ ছিল না।
শ্রদ্ধেয় আরেকটা বস্তুর কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে–প্রশ্নপত্র।
প্রথম ঘন্টা বাজত রোল নম্বর অনুযায়ী বসার নির্দেশ জানাতে। দ্বিতীয় ঘন্টায় প্রথমে উত্তরপত্র বিলি হোত। এখান থেকে শুরু হোত সিরিয়াস হওয়ার পালা। কেননা এরপরই আসবে চরমক্ষণ–প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়া।
কলম বের করে নাম লিখে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতাম। কর্মচারিদের কেউ একজন ক্লাসে এসে শিক্ষকের হাতে তুলে দিতেন একটা বড় খাম। ক্লাস শুদ্দু সবার দৃষ্টি তখন ওই খামের দিকে। স্যার ধীরেসুস্থে খাম খুলে বিলি করতে শুরু করতেন। প্রথম বেঞ্চে প্রশ্নপত্র দেয়া মাত্র পরের বেঞ্চগুলোয় শুরু হয়ে যেত উসখুস, কেমন এসেছে রে ? কমন রয়েছে কিছু?
প্রশ্ন পাওয়া মাত্র প্রণাম করে লেখা শুরু করত তো মাত্র কয়েকজন, বাদবাকিরা প্রণাম করে আগপাশতলা পড়ে নিতো। যারা তখনও প্রশ্নপত্র হাতে পেত না তাদের কাজ ছিল সামনের মুখগুলো যাচাই করা। মুখে হাসি, নাকি গাম্ভীর্য? এবং প্রশ্নপত্র হাতে না পাওয়া অবধি ঘন ঘন কপালে হাত ঠোকা জারি থাকত। আর প্রশ্নপত্র হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেলে? ওহ, তাহলে তো নরকবাস অনিবার্য। শত প্রণামেও রেহাই মিলবে কিনা সে সংশয়ে মনের ভেতরে কাঁটা খচখচ করত।
আমাদের আগের প্রজন্মে গণ টোকাটুকি কিংবা পরীক্ষা ভন্ডুলের রেওয়াজ থাকলেও প্রশ্ন ফাঁসের কোনো ইতিহাস ছিল না। আমাদের সময়ে তিনটের কোনোটাই নয়। প্রশ্নপত্র ছিল আমাদের কাছে অলৌকিক এক বস্তু। পরীক্ষার দিন, বড় জোর আগের দিন, স্বর্গের ভল্ট থেকে সরাসরি নেমে এসে ঢুকে পড়ে হেডস্যারের আলমারিতে। নির্দিষ্ট সময় এলে আলমারি খুলে সেগুলো বিলি করা হয়। সুতরাং প্রশ্ন কেমন হবে, সহজ নাকি কঠিন, সেটা নির্ভর করবে কার কতটা পুণ্য সঞ্চিত রয়েছে তার ওপরে। অতএব প্রশ্নপত্রকে প্রণাম করে সব পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে না নিলে কারুর রেহাই আছে?
বহু বছর পর, যখন সাহিত্য পত্রিকার সুবাদে ঘনঘন প্রেসে যাওয়া শুরু করেছি, মালিক তো বটেই কম্পোজিটর, মেশিন ম্যান, সবার সঙ্গেই কিঞ্চিতাধিক দোস্তি হয়েছে তখন অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কয়েকটা কাগজ এনে প্রেসমালিক অনুরোধ করেছিলেন, আপনাদের প্রুফ উঠতে তো একটু দেরী আছে ততক্ষণ এই প্রুফটা একটু দেখে দিন না।
অনুরোধের মোড়ক থাকলেও মূলত ওটা আদেশই ছিল। যেহেতু ধারে কাজ করাতে হয় এবং ধারশোধেরও কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকে না তাই প্রায়শই ওরকম আদেশ পেতাম।
পাতাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতেই অজ্ঞান হওয়ার জোগাড়। আমার ছেড়ে আসা স্কুলের ক্লাস এইটের ইংরেজির প্রশ্নপত্র! এবং আগামী বার্ষিক পরীক্ষার!
–এখানে ছাপা হয় নাকি আমাদের স্কুলের কোশ্চেন পেপার?
আমার বিস্ময় দেখে হেসেছিলেন প্রেসমালিক।
–এই প্রথম নাকি? কুড়ি বছর ধরে ছাপছি।
–সব ক্লাসের?
–সব ক্লাসের। সব বিষয়ের।
আমাদের রাস্তা থেকে মোটে তিন রাস্তা দূরে থাকা আবাল্য পরিচিত প্রেসটা এরপর নিমিষে আমার কাছে হয়ে পড়েছিল স্বর্গ। প্রেসমালিক হয়েছিল প্রশ্নপত্রের দেবতা।
আর আমি নিজে?
থাক সে কথা। বলার শুধু এটুকুই যে, এরপর প্রুফটা টেনে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে ছিলাম। অভ্যেস বশত।
(চলবে……)